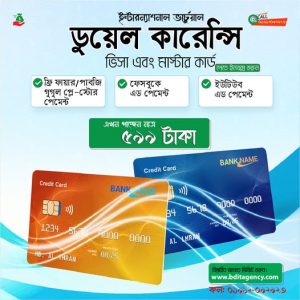বাংলাদেশের রাজনীতিতে নির্বাচন পদ্ধতি নতুন করে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে। সম্প্রতি জামায়াতে ইসলামী তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন যে, সংসদ নির্বাচনে আসন বণ্টন হতে হবে ভোটের অনুপাতে, অর্থাৎ প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (পিআর) পদ্ধতিতে। এই দাবির প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি দৃঢ়ভাবে এই পদ্ধতির বিরোধিতা করছে। বিতর্কটি শুধুমাত্র নির্বাচনী নীতি নিয়ে নয়, এটি ভবিষ্যৎ নির্বাচনের প্রস্তুতি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং দলের শক্তি কাঠামোর উপরও গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।
পিআর পদ্ধতি হলো এমন একটি নির্বাচনী ব্যবস্থা যেখানে ভোটার সরাসরি প্রার্থীকে নয়, দলকে ভোট দেন। যে দল মোট ভোটের কত শতাংশ পাবে, তার অনুপাতে সংসদে আসন বরাদ্দ হয়। উদাহরণস্বরূপ, ৩০০ আসনের সংসদে কোনো দল যদি ১০ শতাংশ ভোট পায়, তবে তার ৩০টি আসন বরাদ্দ হবে। এই পদ্ধতি ছোট দলগুলোরও সংসদে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে এবং একক দল বা বৃহৎ দলের মনোপলি হ্রাস করতে সহায়ক। বিশ্বের ৯১টি দেশে এই পদ্ধতি কার্যকর, এবং এ অঞ্চলে নেপাল ও শ্রীলঙ্কার উদাহরণ উল্লেখযোগ্য।
পিআর পদ্ধতির সুবিধা
ছোট দলগুলোর সংসদে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা: এটি রাজনৈতিক বহুমুখিতা বা প্লুরালিজম বৃদ্ধিতে সহায়ক। ছোট দলও ভোটের মাধ্যমে সংসদে আসন পেতে পারে।
ভোটের অংশগ্রহণ ও ন্যায্যতা বৃদ্ধি করা: প্রচলিত ‘ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট’ পদ্ধতিতে সংখ্যালঘু ভোটের প্রতিফলন কম হয়, পিআর-এ তা পূর্ণ হয়।
বৃহৎ দলের একক মনোপলি হ্রাস করা: ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় থাকে, একক দল সব আসন দখল করতে পারে না।
নতুন ও উদীয়মান দলের সুযোগ বৃদ্ধি: নতুন দলগুলোও ভোটের মাধ্যমে সংসদে অংশগ্রহণ করতে পারে, যা গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা বাড়ায়।
ভোট শোষণ কমানো: প্রভাবশালী পরিবার বা গোষ্ঠীর দ্বারা ভোট শোষণ কিছুটা হ্রাস পায়, কারণ আসন বরাদ্দ সম্পূর্ণ ভোটের অনুপাতে।
পিআর পদ্ধতির অসুবিধা
ভোটারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ নেই: ভোটার প্রার্থী নয়, দলকে ভোট দেয়। ফলে নির্বাচিত প্রতিনিধি এলাকার জনস্বার্থের সঠিক প্রতিনিধি হতে নাও পারে।
দলের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি: দল ইচ্ছেমতো প্রার্থী মনোনয়ন দিতে পারে। স্বামী-স্ত্রী, আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠদের মনোনয়ন দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
রাজনৈতিক স্বার্থ ও চাপ: ক্ষমতার ভাগাভাগি বা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে দল বা সরকারের কোনো অংশ পিআর দাবির ব্যবহার করতে পারে। বিএনপি এটি ‘নতুন ইস্যু’ উত্থাপন করে নির্বাচন পেছানোর কৌশল হিসেবে দেখছে।
বৃহৎ দলের জন্য চ্যালেঞ্জ: ছোট দলগুলোরও আসন থাকায় বৃহৎ দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করতে পারবে না।
প্রক্রিয়ার জটিলতা: ভোটের হার, আসন বরাদ্দ ও গণনা প্রক্রিয়া জটিল, সাধারণ মানুষের জন্য বোঝা কঠিন হতে পারে।
স্থানীয় সমস্যা ও জনমতের প্রতিফলন কম: যেহেতু ভোট প্রার্থী নয়, দলের ওপর, তাই এলাকার বিশেষ সমস্যা বা স্থানীয় জনমতের সঠিক প্রতিফলন কম হতে পারে।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, এই বিতর্ক ক্ষমতার ভাগাভাগি ও সুবিধা আদায়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সরকারের ঘনিষ্ঠ কোনো অংশ বা প্রভাবশালী দলের সদস্যরা নির্বাচনের আগে পিআর দাবির মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রভাব তৈরি করতে পারেন। অন্যদিকে জামায়াত দাবি করছে, প্রচলিত পদ্ধতিতে ভোটের ন্যায্যতা কম এবং জনমতের সঠিক প্রতিফলন ঘটছে না। তাদের মতে, ‘কোয়ালিটি নির্বাচন’ নিশ্চিত করতে পিআর প্রয়োজন।
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের লন্ডন বৈঠকের পর এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে সংসদ নির্বাচনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, পিআর পদ্ধতি শুধু ভোটের হিসাব বা আসন বণ্টন নয়; এটি দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, দলের শক্তি কাঠামো এবং জনগণের বিশ্বাসের উপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।
সারকথা পিআর পদ্ধতি নির্বাচনী সংস্কারে সম্ভাবনাময়। এটি ছোট দলগুলোর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে, ভোটের ন্যায্যতা বৃদ্ধি করে এবং বৃহৎ দলের একত্রীকরণ হ্রাস করতে পারে। তবে ভোটারদের সরাসরি অংশগ্রহণের অভাব, দলের মনোনয়ন প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক স্বার্থের প্রভাব এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা। এই সুবিধা-অসুবিধা মিলিয়ে পিআর নিয়ে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে এবং আগামী নির্বাচনের জন্য এটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছে।
খাইরুল ইসলাম আল আমিন
সাংগঠনিক সম্পাদক
বাংলাদেশ অনলাইন সংবাদপত্র সম্পাদক পরিষদ (বনেক)